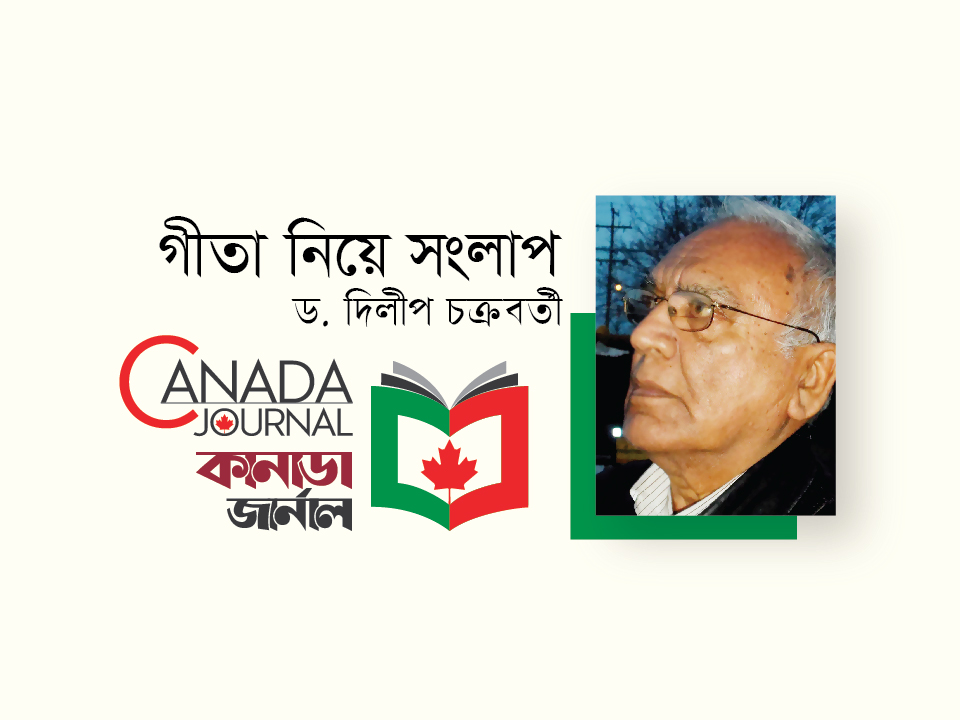গীতা নিয়ে সংলাপ
‘শিক্ষিত’ বলতে আমরা সাধারণত দুই ধরনের পড়াশোনা করা মানুষকে বুঝি – এক্সটেন্সিভ স্টাডি (extensive study) করা এবং ইন্টেসিভ স্টাডি (intensive study) করা। এক্সটেন্সিভ স্টাডি বলতে আমরা বুঝি সকল কিছুর অল্পঅল্প জানা (to know something of everything) আর ইন্টেসিভ স্টাডি বলতে বোঝায় কোনো কিছুর গভীরে গিয়ে জানা (to know everything of something)। মজার বিষয় হচ্ছে এই দুইটি সত্তা যুগপৎ বিদ্যমান এমন মানুষ খুব কম দেখা যায়।
যেমন, আমি আমার নিজের সম্বন্ধে বলতে পারি যে একটা সময় আমার একটা ফুলিশ নোশন ছিল – সবকিছু জানবো। যাকে আধুনিক অনেক ছেলে মজা করে বলে সেক্স থেকে শেক্সপিয়র (from sex to Shakespeare) জানবো। সেই ফুলিশ নোশনের বশবর্তী হয়ে আমি এককালে ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত, ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জীববিদ্যার মতো প্রায় সকল বিদ্যা প্রকৃত অশিক্ষিতের মতন রপ্ত করে ফেলার চেষ্টা করেছি। তার নিট ফল হয়েছে যে আমার কোনো বিদ্যাই রপ্ত হয়নি। সব বিদ্যায় আধাখেচরা হয়েছে। কিন্তু বোধ আমার যখন হলো তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। সত্যি কথা বলতে আমি পড়েছি বেশি, তুলনায় বুঝেছি কম এবং আমি যে বুঝিনি সেটাও বুঝিনি।
ফলে আমি সবসময় সেই মানুষকে শ্রদ্ধা করেছি যার একই সঙ্গে আছে এক্সটেন্সিভ স্টাডি এবং ইন্টেসিভ স্টাডি আছে। এই শ্রেণিতে প্রথমে যে নামটা আমার হাতের কাছে উপস্থিত সেটি হলো সুব্রত কুমার দাস। আমরা মজা করে সুব্রতকে ‘তথ্যসম্রাট’ বলি অর্থাৎ ও যার ভেতরে ঢোকে আক্ষরিক অর্থে তার পেটা-পিত্তি গেলে দেয়। ওর গ্রন্থ পাঠের ব্যাপকতা এবং নিষ্ঠা দেখলে ওকে কুর্নিশ না করে পারা যায় না।
সুব্রতর এই রূপটা আমি আজ সকালে আবার দেখলাম। আমি জানি যে, রোজ সামান্য কিছু না পড়লে আমার ঠিক শান্তি হয় না। কিন্তু আমি আগেই বলেছি যে আমার পড়ার বিষয়ের মধ্যে কোন সাজুয্য নেই। আমি এই মুহূর্তে শেক্সপিয়র পড়তে পড়তে পরের মুহূর্তে ক্লাইমেট চেঞ্জ বা কার্বন এমিশন নিয়ে পড়তে আরম্ভ করতে পারি। আমার বন্ধুরা ঠাট্টা করে বলতো দিলীপ একটা ঠোঙা পেলেও পড়ে। আমি অনেক পরে এটা অনুধাবন করেছি যে আমার পড়ার মোশন ছিল কিন্তু ডিরেকশন ছিল না। ফলে মা সরস্বতীর অঙ্গনে আমি কলুর বলদের মতন ঘুরেই গেছি। এক পাও এগোতে পারিনি।
আমি কাল সকালে পড়ছিলাম শেক্সপিয়র – উৎপল দত্তের মননে। আর আজ একটু আগে পড়ছিলাম গীতা। সেটা শেষ হওয়ার আগেই আমার ভগবদ-গীতার ওপর আক্রমণ অর্থাৎ হঠাৎ সুব্রতর ফোন। ও কিন্তু জানতো না যে আমি গীতা পড়ছি এবং এমন নয় যে ও সেটা জেনে মনে মনে চিন্তা করে রেখেছে গীতা সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলবে। ঘটনা কোনোক্রমেই তা নয়। ও হঠাৎই জানলো যে আমি গীতা পড়ছি এবং যেইমাত্র সুব্রত জানলো যে আমি গীতা পড়ছি ও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে গীতা সম্বন্ধে এমন অনেক সারগর্ভ কথা বলল যে আমি আক্ষরিক অর্থেই ঋদ্ধ হলাম।
সবচেয়ে অবাক করা কথা, সুব্রত বলল যে আমাদের সকলের পরিচিত ভগবত গীতায় কৃষ্ণের যে সকল উপদেশাবলী সম্বলিত হয়েছে সেটা মানব চরিত্রের অসাধারণ জ্ঞাতা বেদব্যাসের বুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও কল্পনা-প্রসূত। সে আরও বললো, ভগবত-গীতার পূর্বসূরী ঈশ্বর-গীতায় শ্রীকৃষ্ণের নাম-গন্ধও নেই। যদিও আছে নারায়ণ – কৃষ্ণ যে ঈশ্বরের অবতার রূপে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। ঈশ্বরগীতায় মুখ্য – স্বয়ং মহাদেব। তিনিই সেখানে ঈশ্বরের প্রতিভূ। ভগবদ-গীতা যেমন কৃষ্ণ আর অর্জুনের সংলাপ, ঈশ্বরগীতা তেমনি মহাদেব এবং মুনিদের সংলাপ। সুব্রতর এইসব কথা হিন্দুধর্ম বিষয়ে ওর গভীর পাঠেরই পরিচায়ক।
আমরা বুঝতে পারি, বেদব্যাস যথার্থই অনুভব করেছিলেন যে, ভগবানের মুখনিঃসৃত বাণী সাধারণ মানুষকে যতটা প্রভাবিত করবে তার চেয়ে অনেক বেশি প্রভাবিত করবে যদি সেই বাণী মানুষের পরিচিত এবং আপন কোন ব্যক্তির কাছ থেকে আসে। তিনি নির্বাচন করলেন কৃষ্ণকে। তিনি খাঁটি ভগবান না, তার ভগবত সত্তার মধ্যে মানবিক খাদ বসানো। তাই তিনি মনুষ্য-রূপী ভগবান অথবা দেবতা-রূপী মানুষ। শ্রীকৃষ্ণ এমন ভগবানের রূপ যে তাঁর আচরণ অনেক বেশি মানব-বান্ধব। তিনি সিচকে চোরের মত ননি চুরি করে খাচ্ছেন, আবার গোপিদের সঙ্গে লীলা করছেন, আবার বিশ্বরূপও দেখাচ্ছেন। একই সাথে তিনি মহাভারতের মহাযুদ্ধের মহানায়কের ভূমিকা পালন করছেন। এই শ্রীকৃষ্ণ তো জনসাধারণের খুব পরিচিত যাকে হাত দিয়ে ছোঁয়া যায়, যার সাথে রঙ্গ-রসিকতা করা যায়। আবার যার থেকে জীবন দর্শন নিয়ে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ শোনা যায়। অন্যদিকে শ্রীরামচন্দ্রও অবতার, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মত ‘মাই ডিয়ার’ নন। তিনি মর্যাদা পুরুষোত্তম। তাঁকে শ্রদ্ধা করা যায়, দূর থেকে সশ্রদ্ধ প্রণাম করা যায়, কিন্তু কৃষ্ণের মতন আপন বা সখা ভাবা যায় না।
সুব্রত অবলীলায় বলে গেল ব্যাসগীতার কথাও। আমাদের অনেকেই ভগবদ-গীতা ছাড়াও অন্যান্য গীতার কথা শুনেছি, কিন্তু সেই গীতাগুলোর কোনোটাই পড়েছি বলে মনে হয় না। সুব্রতর বিশেষত্ব এই যে, ও সেগুলো সংগ্রহ করেছে। সেগুলোকে আত্মস্থ করেছে, এবং সবগুলো গীতা নিয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা তৈরিও করেছে। আর সে কারণেই ওর পাঠ হয়ে উঠেছে এক্সটেন্সিভ রিডিং।
সুব্রত বললো, ব্যাসগীতাতে যাই বলা হয়েছে তা হয়েছে কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাসের বয়ানে। সেই বয়ানে যা যা অন্তর্ভুক্ত তাঁর সবই আসলে কর্মযোগের বিষয়। যেমন বলা যায়, ঈশ্বরগীতায় যা যা অন্তর্ভুক্ত তা আসলে জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের বিষয়। বলে রাখা যেতে পারে যে, ঈশ্বরগীতা এবং ব্যাসগীতা রয়েছে কুর্মপুরাণে, যেমনভাবে ভগবদ-গীতা রয়েছে মহাভারতে।
অদ্ভুত এক নিরাসক্তি নিয়ে সুব্রত বললো, বেদব্যাস তাঁর লব্ধ জ্ঞানকে অন্য অনেক লেখকের মতো মার্জনা, পরিমার্জনা করেছেন বছরের পর বছর ধরে। সেই ক্রম-পরিমার্জিত জ্ঞানরাশির চূড়ান্ত প্রকাশ শ্রীমদ্ভগবদগীতা। আর তাই, সেটির প্রকাশ এতো বেশি মর্যাদাসম্পন্ন, এতো গভীর অভিজ্ঞানলব্ধ, এতো অধিক সুদূরপ্রসারী! সুব্রতর ভাষ্যমতে, গীতায় সন্নিহিত জ্ঞান, কোনো বিশেষ অভিনবত্ব ধারণ করে না, বরং ভারতবর্ষীয় সমাজে জনমানসের প্রচলিত সামূহিক জ্ঞানকে (collective conciousness) পরিশীলিত করেই গীতায় পরিবেশন করেছেন বেদব্যাস।
গীতা নিয়ে আমার পুত্রবয়সী সুব্রতর এমন গভীর অনুধ্যান আমাকে যেন নতুন এক আলোকবর্তিকা দান করলো। এক কথায় বলতে গেলে সুব্রত যেন আমার চোখ খুলে দিল। আমি নতুন করে বেদব্যাসের প্রতিভার আভাস পেলাম। বেদব্যাসের অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা এবং জনসাধারণের মনো-বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সম্বন্ধে ওর ধী-শক্তির পরিচয় পেয়ে শ্রদ্ধায় অবনত হলাম।
এক যুগ আগে লেখা সুব্রতর ‘আমার মহাভারত’ বইতে এইসব প্রসঙ্গ আছে। কিন্তু সুব্রতর অনন্যতা এখানেই যে, ও কিন্তু গীতা-মহাভারত বিষয়ে ওর পাঠকে ওখানেই সীমাবদ্ধ রাখেনি। নতুন নতুন গবেষণা আর মূল্যায়ন দিয়ে ও নিজেকে ঋদ্ধ করে চলেছে সবসময়। আর যেমনটি ওর মজ্জাগত, অধিত জ্ঞানকে সবার সাথে সহভাগ করে চলেছে প্রতিনিয়ত।