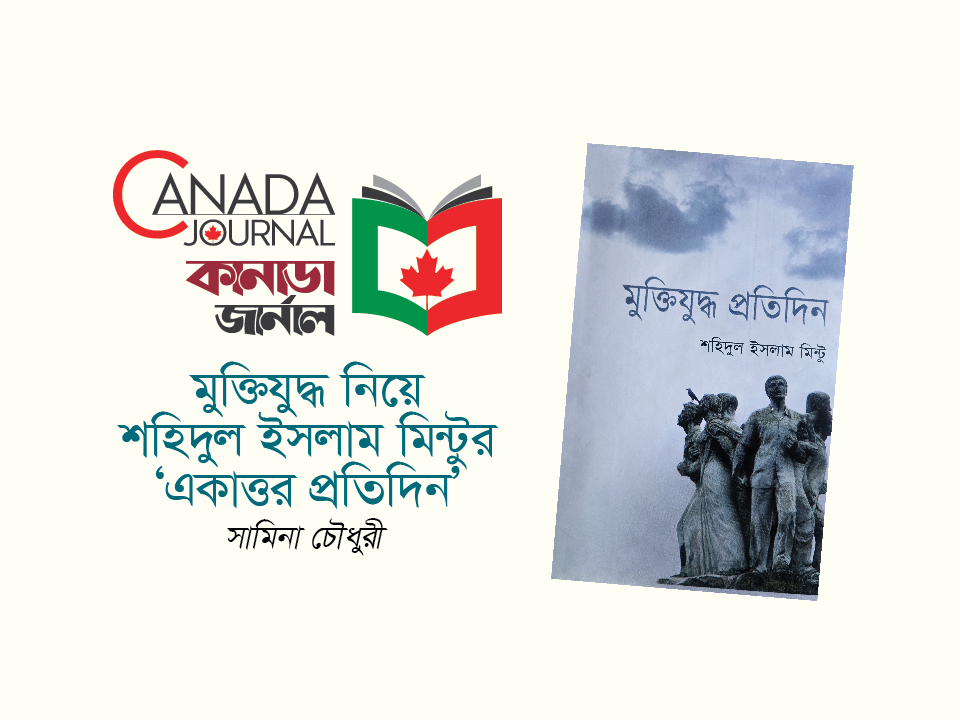মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে শহিদুল ইসলাম মিন্টুর ‘একাত্তর প্রতিদিন’
একটি জাতির ইতিহাস শুধু তার বিজয়ের গল্প নয়, বরং তা তার আত্মত্যাগ, সংগ্রাম ও চেতনার ধারক। যুদ্ধ যেমন একটি ভূখণ্ডের স্বাধীনতা এনে দেয়, তেমনি সেই স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তোলে জাতির মানসিক বিকাশ ও সাংস্কৃতিক চর্চা। তাই দেশজয়ের যুদ্ধের চেয়েও কঠিন হয়ে দাঁড়ায় মানুষকে মানসিকভাবে সুস্থ রাখার যুদ্ধ। এই যুদ্ধের অন্যতম হাতিয়ার হলো রুচিশীল ও সৃজনশীল বিনোদন। সুস্থ বিনোদন যেমন মানসিক চাপ কমায়, তেমনি তা মানুষের মধ্যে সহমর্মিতা, দায়িত্ববোধ ও সৃজনশীলতা জাগিয়ে তোলে। গান, কবিতা, নাটক, সাহিত্যচর্চা, খেলাধুলা – এসবই একটি জাতিকে সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ করে। এই চর্চাকে সামনে রেখে যারা কাজ করেন, তারা নিঃসন্দেহে জাতি গঠনের এক নীরব যোদ্ধা। শহিদুল ইসলাম মিন্টু তেমনই একজন যোদ্ধা – একাধারে লেখক, সাংবাদিক, সম্পাদক, সংগঠক ও মুক্তিযুদ্ধ গবেষক। টরন্টো প্রবাসী শহিদুল ইসলাম মিন্টু সাপ্তাহিক বাংলামেইল পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক এবং উত্তর আমেরিকার প্রথম ২৪ ঘণ্টার বাংলা টেলিভিশন চ্যানেল এনআরবি টিভির প্রধান নির্বাহী। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ১৬টি। মুক্তিযুদ্ধ তাঁর লেখার অন্যতম প্রিয় বিষয়। তাঁর লেখা ‘মুক্তিযুদ্ধ প্রতিদিন’ বইটি একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাধর্মী দলিল, যা ১৯৭১ সালের ১ ডিসেম্বর থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিনের ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে রচিত।
বইয়ের নাম শুনেই ধারণা করা যায়, এটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক একটি গ্রন্থ। স্বাধীনতার ৫৫ বছর অতিক্রম করলেও নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানানো এবং সেই ইতিহাসের আলোকে তাদের মাঝে দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলার প্রয়াস এখনও যথেষ্ট নয়। সঠিক ও গবেষণাভিত্তিক গ্রন্থের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও মূল্যবোধ নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া জরুরি। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলি তুলে ধরার মাধ্যমে যুদ্ধের ভয়াবহতা, নৃশংসতা এবং সেই সময়কার রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট নতুন করে উপলব্ধি করা সম্ভব। এ ধরনের রচনার মাধ্যমে তরুণদের মাঝে সহানুভূতি, সংবেদনশীলতা ও ঐতিহাসিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং তারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতিগত ঐক্যের পথে অগ্রসর হতে পারে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে শহিদুল ইসলাম মিন্টুর মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা ও গ্রন্থ রচনার প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।
‘মুক্তিযুদ্ধ প্রতিদিন’ বইটিতে ১৯৭১ সালের ১ ডিসেম্বর থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত ঘটে যাওয়া প্রতিদিনের ঘটনাবলী উপস্থাপন করা হয়েছে। উত্তাল সময়ের সেই অসংখ্য ঘটনাবলী বিষয়ে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ, বিভিন্ন মানুষের স্মৃতিচারণ, কিছু বিশ্লেষণ, কিছু সরকারী নির্দেশমালা এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কিছু বইপত্রের উদ্ধৃতি বইটির উৎস। পাশাপাশি এই গ্রন্থটি থেকে ১ ডিসেম্বর থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধাদের অগ্রযাত্রার তথ্যাবলীও পাঠক জানতে পারবেন। এসময়টা ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয়ের মাস। প্রতিদিনই তারা হানাদার বাহিনীকে হারিয়ে নতুন নতুন এলাকা দখল করছিল। গ্রন্থের তথ্যানুসারে ১ ডিসেম্বর ভোরে মুক্তিযোদ্ধারা আজমপুর রেলস্টেশনের উত্তরাংশ এবং বিকেলে দক্ষিণাংশ দখল করতে সক্ষম হয়। এসময় বিভিন্ন জায়গায় আলবদর-আলশামস বাহিনীর কর্মীরা সক্রিয় ছিল এবং বিভিন্ন স্থানে তারা সভাসমাবেশ করছিল। সেই সভা সমাবেশে কে কী মন্তব্য করেছিলেন, সেটাও বইটিতে পাওয়া যায়। পহেলা ডিসেম্বরে ঘোড়াশাল ন্যাশনাল জুট মিলের ৯৬ জন কর্মকর্তাকে এক লাইনে দাঁড় করিয়ে নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। বীর মুক্তিযোদ্ধারা ঘোড়াশাল ও টঙ্গী রেলস্টেশনের মাঝে দুই-তিনটি রেলব্রিজ বোমা মেরে উড়িয়ে দিলে হানাদার বাহিনী প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে এই হত্যযজ্ঞ চালায়। হানাদার বাহিনীর নির্মমতার এমনি আরো অনেক ঘটনা নিপুনভাবে চিত্রিত করা হয়েছে গ্রন্থটিতে।
১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা এবং সহায়তার বিষয়টি সর্বজন স্বীকৃত। মুক্তিযুদ্ধকে একটি বৈধযুদ্ধ মনে করেই ভারত মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং দিয়েছে, সীমান্তে উদবাস্তদের সহযোগিতা করেছে এবং বিভিন্ন স্থানে পদাতিক ডিভিশনের সৈন্য মোতায়েন করেছে। ৩ ডিসেম্বর আখাউড়ায় মুক্তিবাহিনীর অবস্থানের উপর দুটি পাকিস্তানী জেট বিমান আক্রমণ চালালে, ভারতীয় জঙ্গি বিমান পাল্টা আক্রমণ চালায়। বলা হয় এই দিনেই সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হয়। ৪ ডিসেম্বর ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৫৭ মাউন্টেন ডিভিশন আখাউড়া এসে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে মিলিত হয় এবং এভাবেই ভারতের সহায়তায় মুক্তিযোদ্ধারা হয়ে ওঠে আরও শক্তিশালী। ২ ডিসেম্বর আমেরিকায় নিযুক্ত পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত আগা শহীদ এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে ইন্দিরা গান্ধীর উপর দোষ চাপিয়ে বলেছিলেন যে ইন্দিরা গান্ধীর প্ররোচনায় পাকিস্তান ও ভারত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের মানুষের স্বাধীন হওয়ার স্বপ্নকে এভাবেই হেয় করেছিল পাকিস্থান। আগা শহীদ বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানের সৈন্য সরিয়ে নেবার ভারতীয় দাবীকে অদ্ভুত বলেও অভিহিত করেন। বিভিন্ন উচ্চপদস্থ ও দায়িত্বশীল কর্মকর্তা এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের মনোভাব ও মতামত কীভাবে যুদ্ধকে প্রভাবিত করেছিল, সে-বিষয়ক গবেষণালব্ধ তথ্যাদি এই গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে।
একটি যুদ্ধ দুটি দেশের মধ্যে সংঘটিত হলেও এতে আন্তর্জাতিক মহল বিভিন্নভাবে জড়িয়ে পড়ে। ১৯৭১ এর ডিসেম্বরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ নিয়ে আগ্রহ তৈরি হয় এবং আন্তর্জাতিক নেতারা এসময় বাংলাদেশের স্বাধীনতার ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। আন্তর্জাতিকভাবে ৫ ডিসেম্বর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই দিনে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বিশেষ সভায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ বন্ধের জন্য উভয় পক্ষকে আহ্বান জানায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন এই প্রস্তাবনার বিরুদ্ধে ভেটো দেয়ার কারণে এই প্রস্তাব পাশ হয় না। সোভিয়েত প্রতিনিধি জ্যাকব বলেন, “এতদিন বাংলাদেশের মানুষগুলো যখন পাকিস্তানি বাহিনীর প্রচন্ড বর্বতার শিকার হয়েছে, তখন কাউকে টু শব্দটি করতে দেখা যায়নি – আজ যখন সে দেশটি মুক্ত হয়ে যাচ্ছে এই বর্বরতাকে খতম করে, তখন সেটা থামানোর জন্য কি উৎসাহ।” (পৃষ্ঠা ৩৫) ৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশকে সমর্থন দানের প্রশ্নে ভারত পাকিস্তানের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়। যুক্তরাষ্ট্র ও চীন মুক্তিযুদ্ধকে সাহায্য করার জন্য ভারত ও সোভিয়েত রাশিয়াকে দোষারোপ করে। ৪ ডিসেম্বর চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী চো পেং ফেই পাকিস্তানের ওপর ভারতীয় হামলার নিন্দা জানিয়ে পাকিস্তানকে দৃঢ় সমর্থন দেয়ার অঙ্গীকার করেন। ৬ ডিসেম্বর ভুটান বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। এভাবেই মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি বিশ্ববাসীর আস্থা তৈরি হওয়ার বীরত্বের গল্প বলেছেন মিন্টু ‘একাত্তর প্রতিদিন’ বইটিতে।
এসময় খুব লজ্জাজনকভাবে হানাদার বাহিনীকে সমর্থনকারী একটি দল সৃষ্টি হয়েছিল যারা স্বাধীনতার বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে সাধারণ নাগরিকদের হত্যায় উল্লাস করেছিল। ৪ ডিসেম্বর চট্টগ্রামে হানাদার ঘাতকদের অভিযানে উল্লাস প্রকাশ করে জামাতে ইসলামী আনন্দ মিছিল বের করে এবং মিছিল শেষে মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করার শপথ নেয়। চাঁদপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, খুলনা সহ আরো অনেক জায়গায় ভারতীয় আক্রমণের প্রতিবাদে সভা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে নেতারা মুক্তিযুদ্ধ সমর্থনে ভারতের ভূমিকার তীব্র নিন্দা জানান। ৬ ডিসেম্বর ভারতীয় হামলা প্রতিহত করতে মুসলিম লীগ ও বিভিন্ন ইসলামী রাজনৈতিক দল বিশেষ মোনাজাত আহবান করে। গ্রন্থটি থেকে পাঠক জানতে পারবেন রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর লেখা কবিতার ‘সেই পুরানো শকুনরা’ কীভাবে ১৯৭১ সালে তাদের ঘৃণ্য কার্যক্রম চালিয়েছিল।
এমনি করেই প্রতিদিন এগিয়ে চলে একটার পর একটা নাটকীয় ঘটনা। যুদ্ধের শেষ মাসে মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয় যখন অপ্রতিরোধ্য, তখন মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর নির্দেশে তৈরি হয় দেশকে মেধাশুন্য করে দেয়ার এক নীল নকশা। দেশ ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় ১৪ ডিসেম্বরের দিকে, যেদিন আল বদর বাহিনীর সহায়তায় পাকিস্তানি নরপিচাশরা হত্যা করে দেশের সূর্যসন্তানদের। ১০ ডিসেম্বর থেকেই বুদ্ধিজীবী হত্যা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু হলেও ১৪ ডিসেম্বর সবচেয়ে বেশি হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়। ঘাতকের হাতে প্রাণ হারান শহীদুল্লা কায়সার, মুনীর চৌধুরী, গিয়াস উদ্দিন আহমেদ, সন্তোষ ভট্টাচার্য, জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা, রাশিদুল হাসান সহ আরো অনেক বুদ্ধিজীবী। এই হত্যায় সহায়তা করেছিল পাকিস্থানপন্থী দলের দোসরেরা, যাদের বিচার আজো অসমাপ্ত রয়ে গেছে।
শহিদুল ইসলাম মিন্টু দক্ষ গবেষকের মত তৎকালীন বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যাবলী, বিভিন্ন মানুষ ও মুক্তিযোদ্ধাদের দেয়া স্মৃতিবিবরণী ও স্বাক্ষাতাকার, ঔপন্যাসিক রাবিয়া খাতুনের স্মৃতিচারণ, শহীদ জননী জাহানারা ইমামের লেখা ‘একাত্তরের দিনগুলি’ এবং আরো বিভিন্ন রকমের উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে বইটিতে উপস্থাপন করেছেন, যা তরুণ প্রজন্মের জন্য একটি অসামান্য দলিল হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। বইটিতে উপস্থাপিত ১৬ দিনের ইতিহাস পড়তে পড়তে পাঠকের মনে হবে তারা যেন ৭১ সালের সেই ঘটনাবহুল, উত্তেজনাময় ডিসেম্বর মাসে ফিরে গেছেন। যারা মুক্তিযুদ্ধের পরে জন্মগ্রহণ করেছেন, বইটি পড়ার সময় তারা বুঝতে পারবেন যুদ্ধকালে দেশকে কতটা বিপদের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়; কতটা বীরত্বের সাথে লড়াই করতে হয়; এবং দেশের মানুষের প্রতি কী পরিমান সহমর্মিতা দেখাতে হয়।
বইটিতে মোট ১৬টি অধ্যায় আছে। প্রতিটি অধ্যায়ের চমৎকার শিরোনাম পাঠককে সেই দিনটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি জানাবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ১৩ ডিসেম্বরের অধ্যায়টির নাম ‘চীনের কাছ থেকে সামরিক সাহায্যের শেষ আশাও বিরহিত হলো’ পড়েই পাঠক এইদিনটির মূল ফোকাসটি বুঝতে পারবেন, যা বইটিকে করেছে সহজপাঠ্য। সব শেষ অধ্যায়ের নাম ‘তিন দিক থেকে ঢাকায় প্রবেশ করলো মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী’। এই শিরোনাম পাঠককে মুক্তিযুদ্ধের চুড়ান্ত বিজয়ের দিনটি সম্পর্কে ধারণা দেবে। বইটির প্রায় প্রতিটি অধ্যায়েই জাহানারা ইমামের লেখা ‘একাত্তরের দিনগুলি’ থেকে উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। শেষ অধ্যায়ে পাঠক জানতে পারবেন জাহানারা ইমাম অল্প অল্প করে নিত্য প্রয়োজনীয় খাবার বাজার থেকে কিনে ছোট ছোট প্যাকেট বানিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সরবরাহ করার জন্য জমা করে রাখতেন। ১৪ ডিসেম্বর জাহানারা ইমামের স্বামী শরীফ ইমাম মারা যান। ১৬ ডিসেম্বরে বিজয় উৎসবের দিন ছিল শরীফের কুলখানি। জাহানারা ইমাম লিখেছেন, “যুদ্ধ কি তাহলে শেষ? তাহলে আর কাদের জন্য সব রসদ জমিয়ে রাখব? আমি গেস্টরুমের তালা খুলে চাল, চিনি, ঘি, গরম মশলা বের করলাম কুলখানির জর্দা রাঁধবার জন্য। … রাতের রান্নার জন্যও চাল, ডাল, আলু, পেয়াজ ইত্যাদি এখান থেকেই দিলাম। আগামীকাল সকালের নাস্তার জন্যও ময়দা, ঘি, সুজি, চিনি, গরম, মসলা এখান থেকেই বের করে রাখলাম।” (পৃষ্ঠা ৭২) গ্রন্থটি থেকে পাঠক জানতে পারবেন কী অসাধারণ শক্তি নিয়ে এই মহিয়সী নারী নিজের শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করে জীবনকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন, হয়ে উঠেছেন বাংলাদেশের সকল মানুষের জননী।
শেষ অধ্যায়ে মিন্টু লিখেছেন, “বিশ্বের মানচিত্রে উদিত হলো একটি দেশ –
বাংলাদেশ। এখনকার প্রজন্ম জ্ঞান হয়ে বাংলাদেশকে দেখছে। কেবল দেখেনি এর পিছনে ত্রিশ লাখ মানুষের আত্মোৎসর্গ। আর কোটি কোটি মানুষের দুঃখ, কষ্ট, নির্যাতন ত্যাগতিতিক্ষা।” (পৃষ্ঠা ৭০) যুদ্ধের ৫৫ বছর পেরিয়ে গেলেও আমরা আজো আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারিনি। কাজেই আমাদের সামনে এখন আরেকটি যুদ্ধ – দেশ গড়ার যুদ্ধ। যথাযথ গবেষণার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ, লক্ষ্য, এবং চেতনা সম্পর্কে আলকপাত করে নতুন প্রজন্মকে দেশপ্রেম এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে যাতে তাদের মাঝে জাতীয়তাবাদী চেতনার বহিপ্রকাশ ঘটে। সাহসী, আত্ম-মর্যাদাশীল এবং আত্ম-বিশ্বাসী একটি নতুন প্রজন্মই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে আলোর পথে, সেই প্রত্যাশা রেখে শহিদুল ইসলাম মিন্টুকে তার মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণার জন্য অভিবাদন জানাই এবং পাঠকের পক্ষ থেকে এই মহান অর্জন নিয়ে আরো লেখার অনুরোধ জানাই।