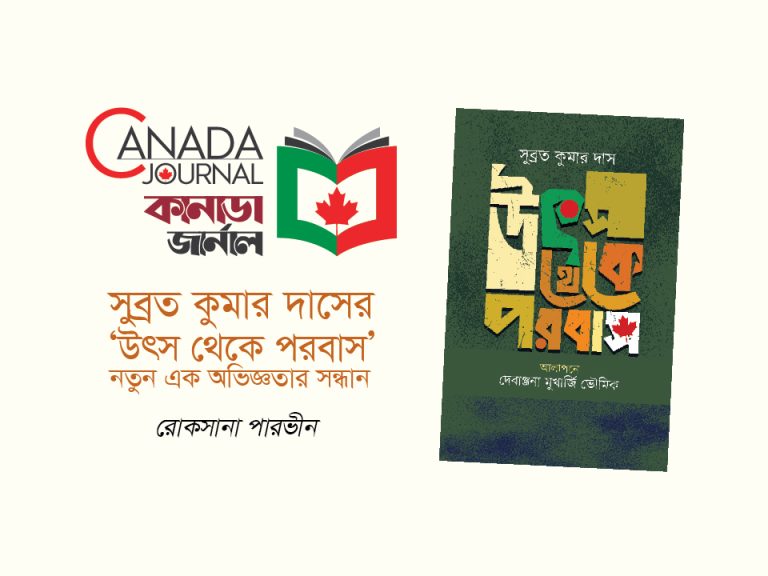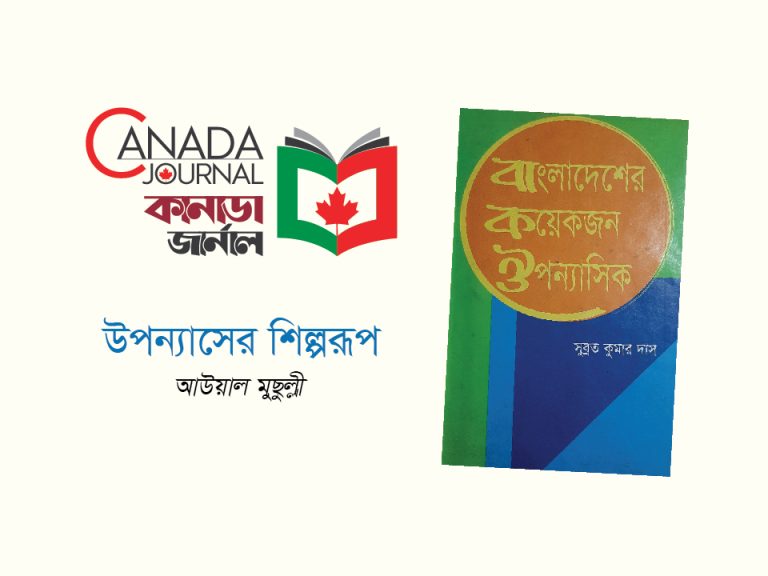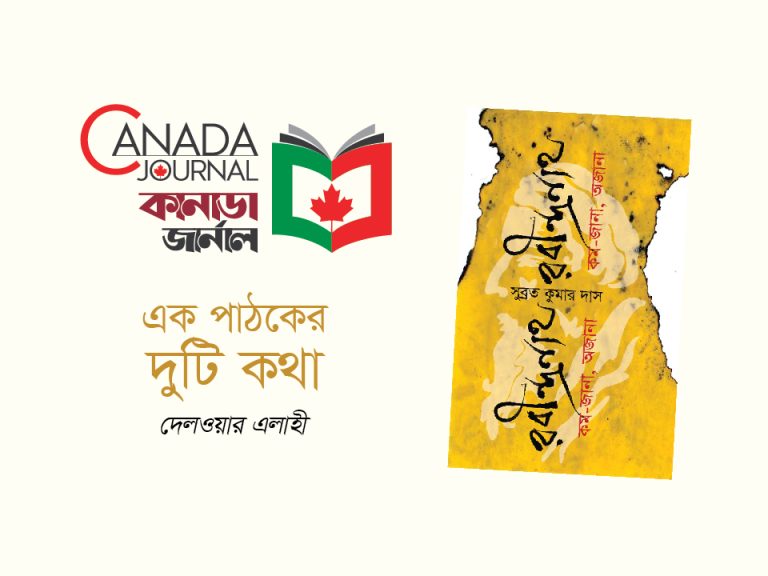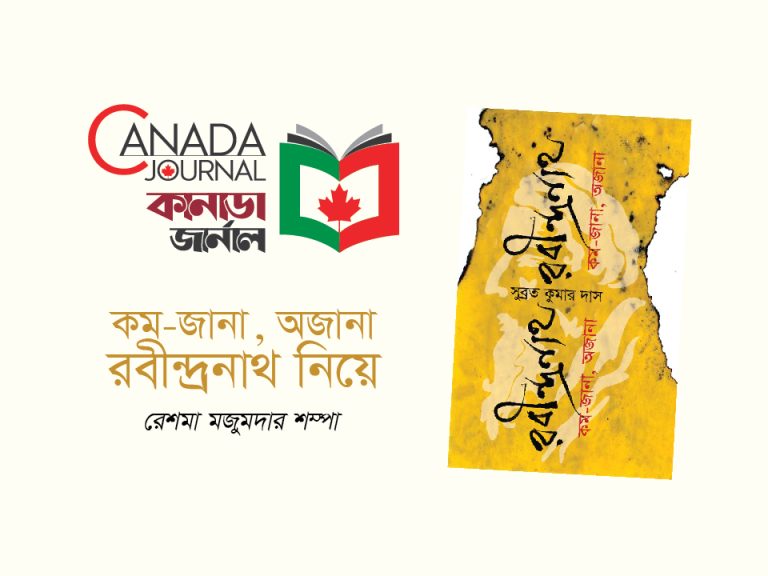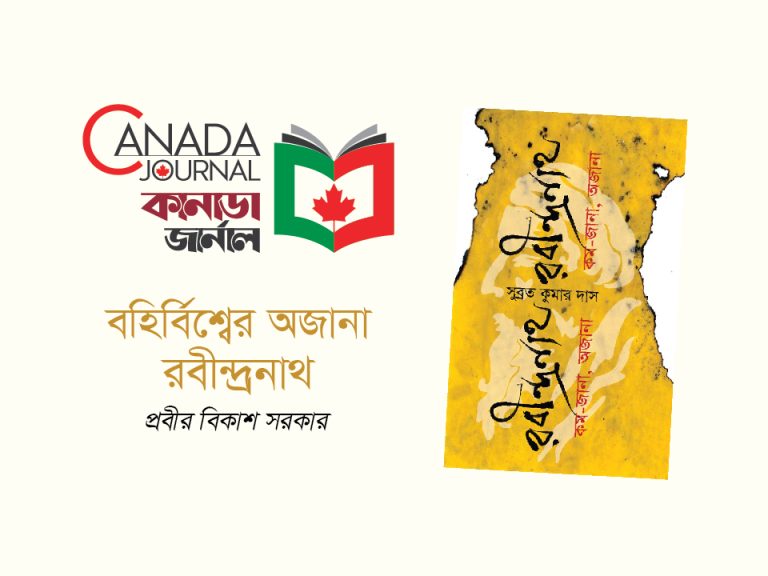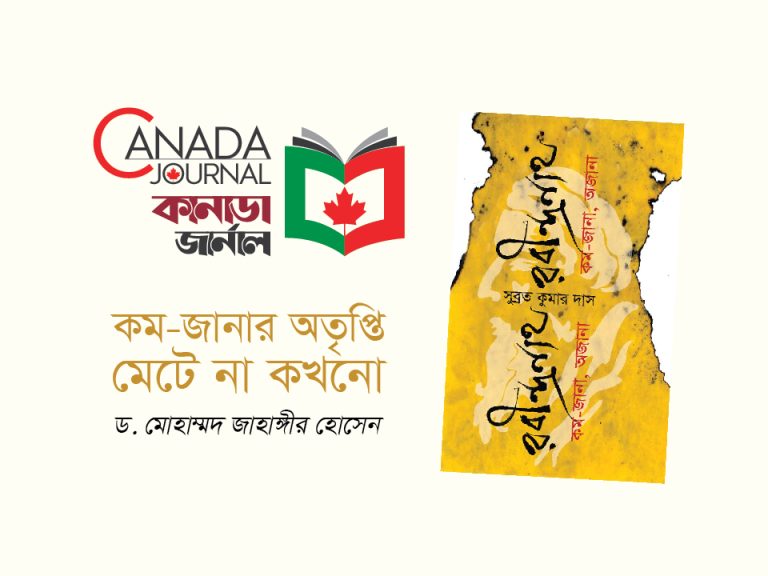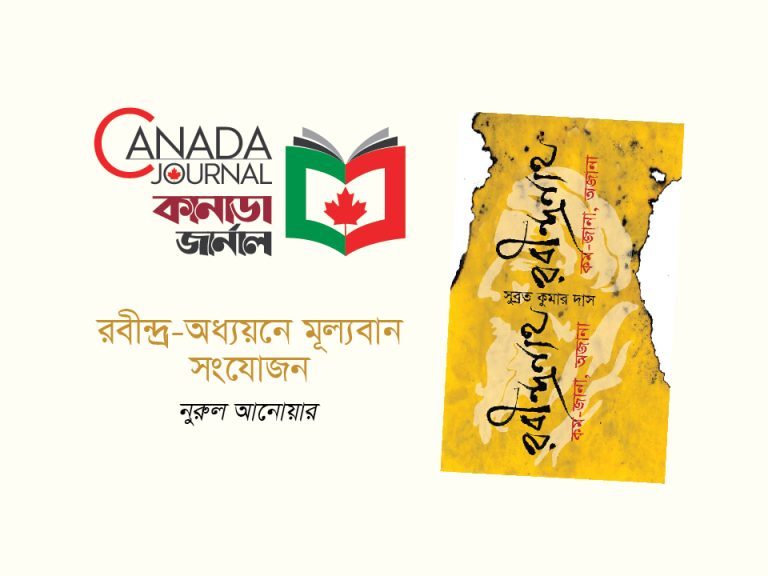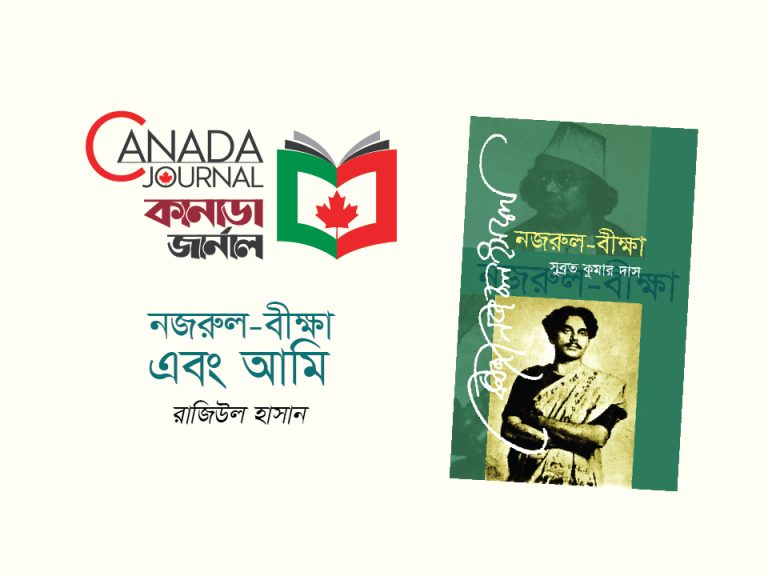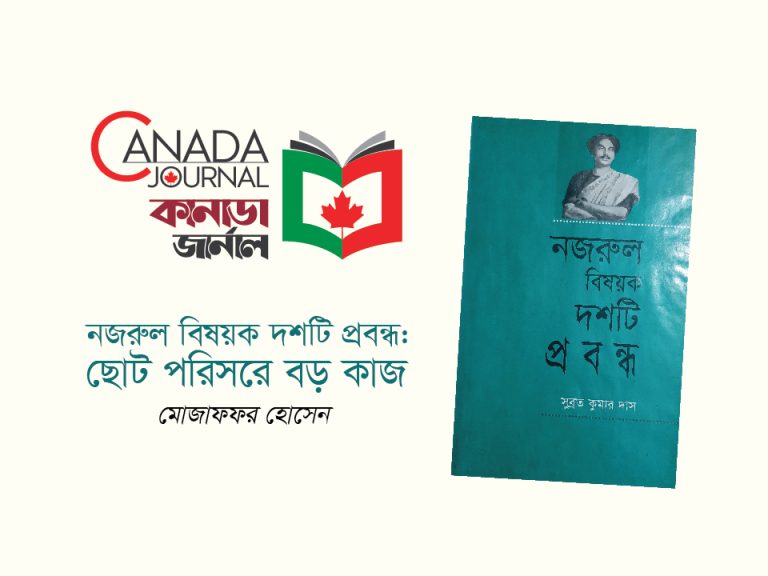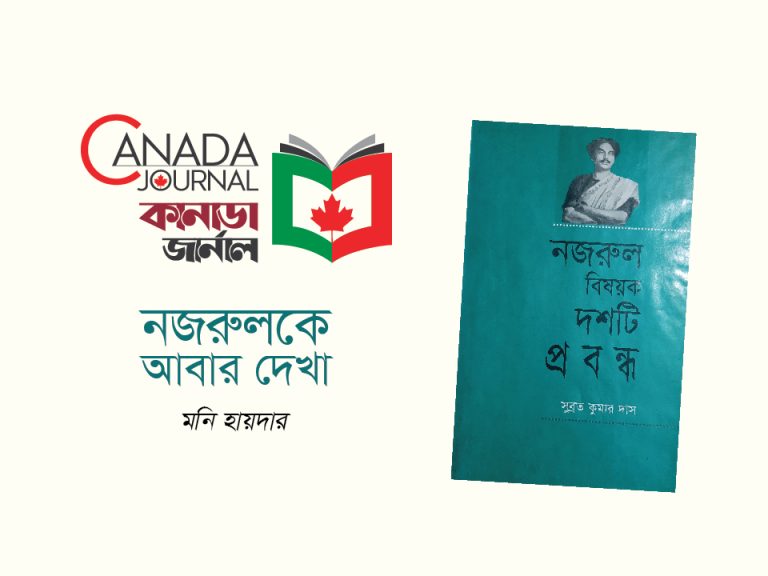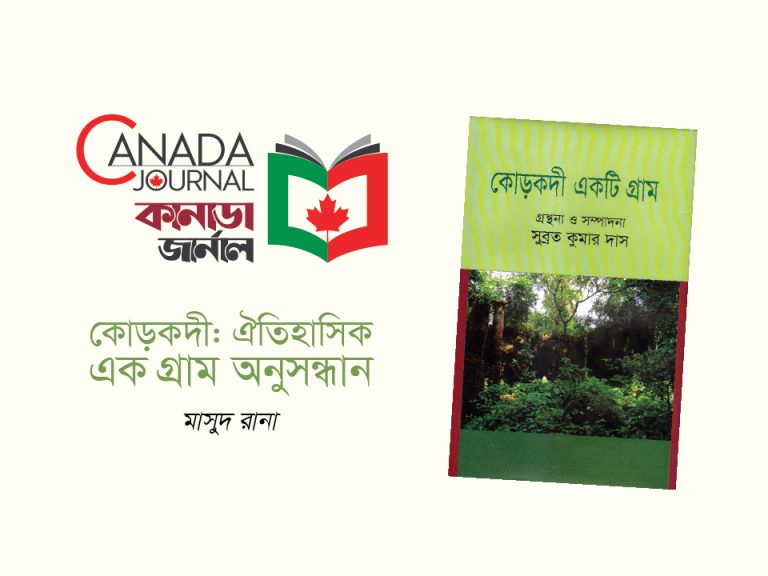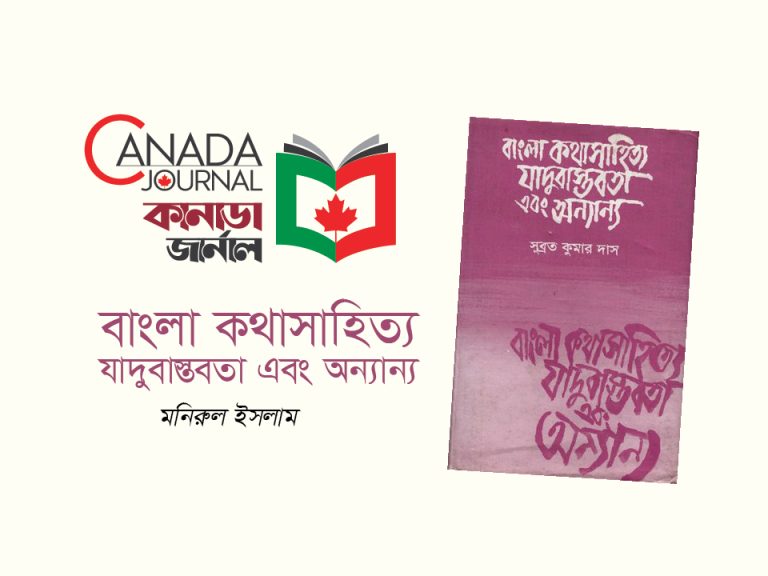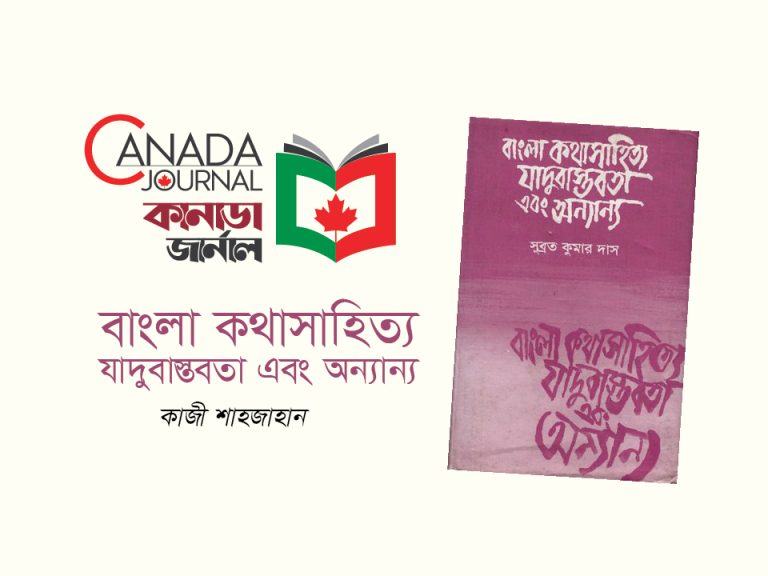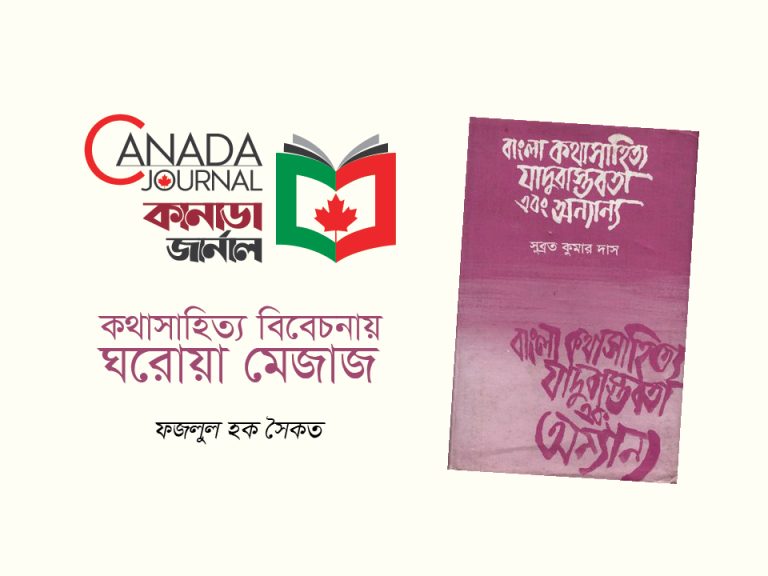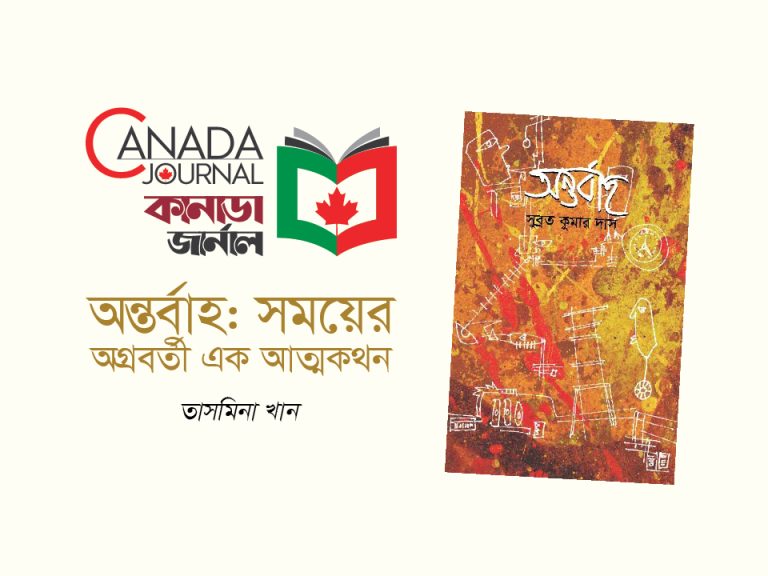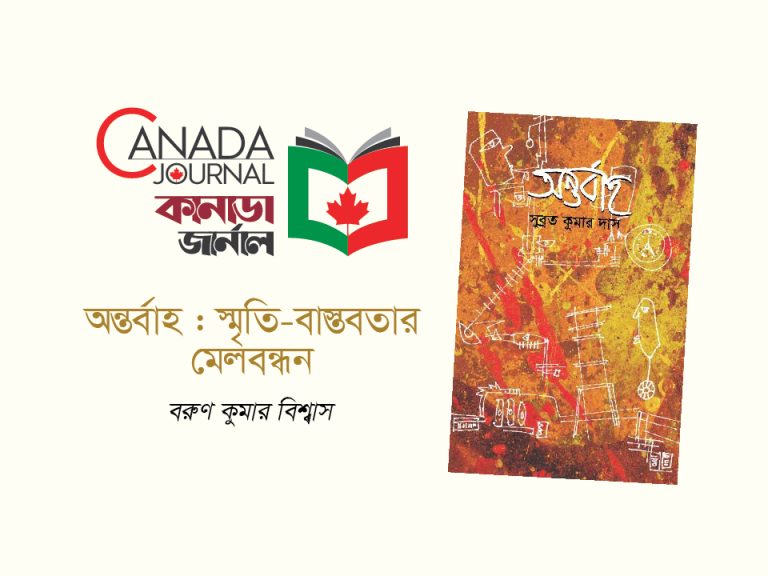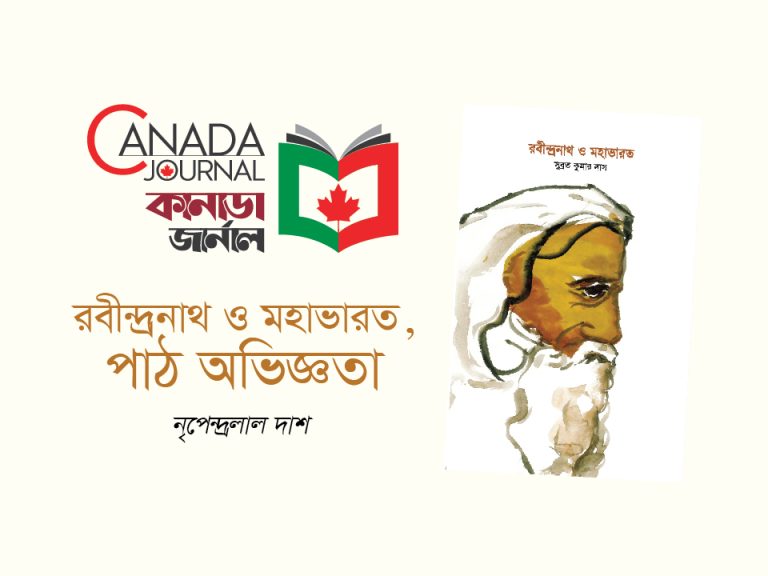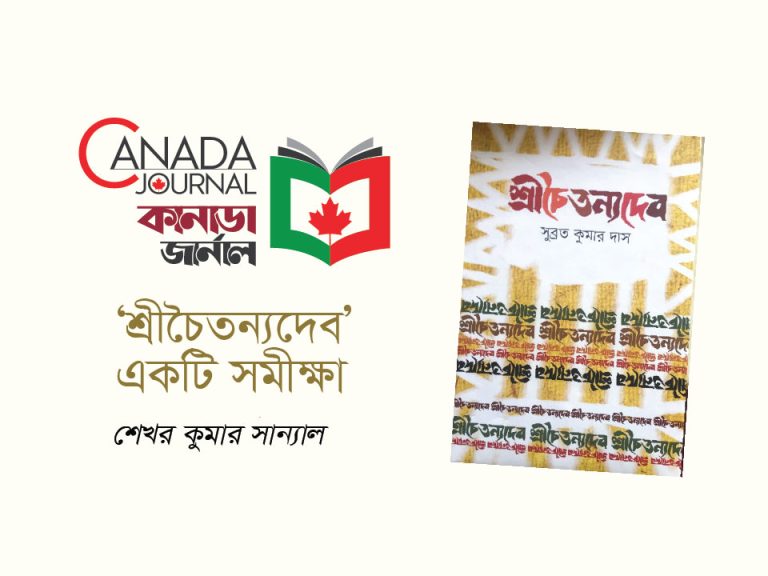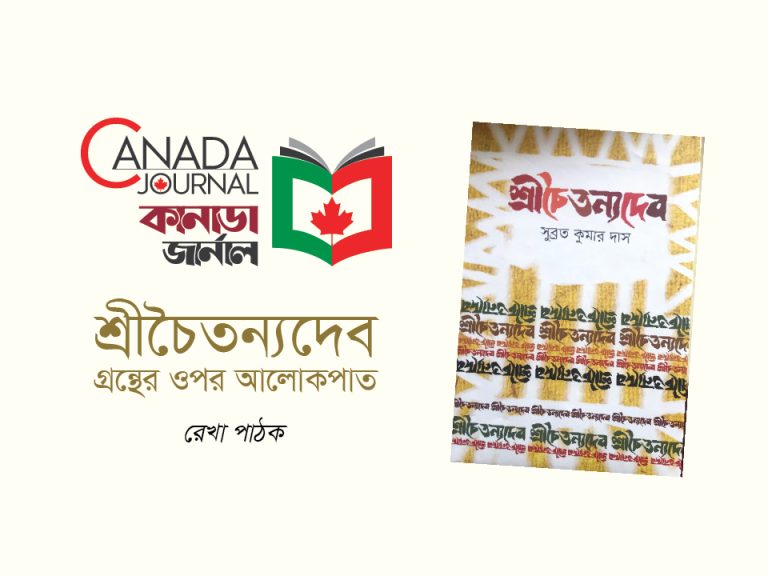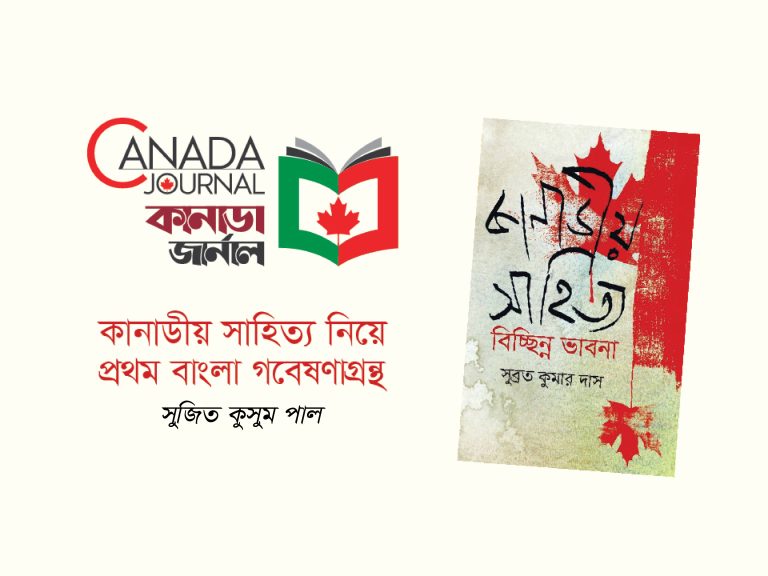সুব্রত কুমার দাসের ‘উৎস থেকে পরবাস’: নতুন এক অভিজ্ঞতার সন্ধান
২০২১ সালে সারা কানাডায় যে ২৫ জন শ্রেষ্ঠ অভিবাসীর ৭৫ জনের যে সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রকাশিত হয় তার মধ্যে লেখক, গবেষক ও সংগঠক সুব্রত কুমার দাস একজন। তাঁর আত্মজীবনীমুলক গ্রন্থ ‘উৎস থেকে পরবাস’ পড়লাম। পুরো বইটিই বিভিন্ন সময়ের ফোনালাপন সাক্ষাৎকার। এই বইটি পাঠ ছিল আমার এক নতুন অভিজ্ঞতা। দেবান্জনা মুখার্জি ভৌমিকের সহজ, সরল, বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্নের মাধ্যমেই শ্রদ্ধেয় সুব্রত কুমার দাস বর্ণনা করেছেন তাঁর শিকড় থেকে বেরিয়ে এসে এখন পর্যন্ত শাখা প্রশাখায় বেড়ে উঠার গল্প।